
‘ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী’, এই একটি উচ্চারণে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকা আর দেবী দুর্গাকে অভিন্ন করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তেমনটা করেননি। দেশকে দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে এক করে দেখার ব্যাপারে ভীষণ আপত্তি ছিল তাঁর।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্গজীবনের সকল রঙ্গে যাঁর প্রবল উপস্থিতি স্বীকৃত এবং আদৃত, সেই রবি কবি কি বাঙালির প্রাণের উৎসব থেকে শেষ পর্যন্ত বিযুক্ত করতে পেরেছিলেন?

এই প্রশ্নের নির্দ্বিধ উত্তর একটাই। সেটা হল ‘না’। রবীন্দ্রনাথ কোনও ভাবেই নিজের রচনায় দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গ উপস্থাপন থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি। ছড়া থেকে গানে, কবিতায় গল্পে এবং উপন্যাসে, সৃজনের যাবতীয় বিভঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, তুলে ধরেছেন, গেঁথে দিয়েছেন।
কারণ, সমাজমনস্ক এই স্রষ্টা জানতেন দুর্গাপুজো বাদ দিলে বঙ্গজীবনচর্যা কীটদষ্ট অসম্পূর্ণতায় আক্রান্ত হয়। নৈকষ্য বাঙালিয়ানা অধরা থেকে যায়। আচার্য সুকুমার সেন যাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘‘রবীন্দ্রনাথের মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে সুখে-দুঃখে জীবনে-মরণে সমদৃষ্টি মান জীবনভাবুক কবি ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই’’, তিনি এমনটা হতে দেন কী করে!

ফলে, যা হওয়ার তাই-ই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে নানাভাবে বিচিত্র বিভঙ্গে দুর্গাপুজো প্রসঙ্গ চলকে চলকে উঠেছে।
যেমন ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাসে।



এখানে শারদীয় পুজো পরোক্ষভাবে উল্লিখিত। আর সেই শরতের আনন্দ প্রহরে রমেশের চোখে কমলার পরিবর্তন, নতুন ভাবে তাকে চেনার আবহ, ভীষণ, ভীষণই তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। এখানে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন ‘অনতিতপ্ত আশ্বিনের মধ্যাহ্নটি মধুর হইয়া উঠিয়াছে—আগামী ছুটির উল্লাস এখনই যেন আকাশকে আনন্দের আভাস দিয়া মাখাইয়া রাখিয়াছে’ তখন আসন্ন আনন্দময়তার ইঙ্গিত নিসর্গের পরিধিতে মুখ গুঁজে দেয়। পাঠক-মন তৈরি হয়ে যায় পরবর্তী ঘটনাক্রমকে আহ্লাদে চেটেপুটে নেবে বলে। সেই ঘটনাটি ঘটে শারদীয়ার তাপ ও আলোয় মাখামাখি হয়ে। বিস্ফারিত নেত্রে রমেশ প্রত্যক্ষ করে পরিবর্তিত কমলার রূপবিভা। আর সেই দেখার মাধ্যম হয়ে ওঠে দুর্গাপুজার প্রাক্কালে কোনও এক দ্বিপ্রাহরিক রৌদ্র।
‘‘আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সে ঋজুদেহে ঈষৎ-বঙ্কিম-মুখে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপর শরৎ-মধ্যাহ্নের আলো আসিয়া পড়িল, তাহার মাথায় কাপড় নাই। অগ্রভাগে লাল ফিতার গ্রন্থিবাঁধা বেণীটি পিঠের উপরে পড়িয়াছে, ফিকে হলদে রঙের মেরিনোর শাড়ি তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে আঁটিয়া বেষ্টন করিয়াছে— তখন রমেশ তাহার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল’’। শূককীটের প্রজাপতি হয়ে ওঠার বর্ণিল গৌরবে এভাবে অন্বিত হয়ে যায় শারদীয় প্রহর। দুর্গা গরিমার প্রত্যক্ষতা না থাকলেও শরতের প্রভাতী আলোর আবহে আগমনির পরোক্ষ প্রাসঙ্গিকতা অগোপন থাকে না। বোঝা যায়, কমলা এবার দুর্গা হল। আর হল বলেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ‘‘শরতের আলোক হঠাৎ যেন প্রাণ পাইল, আশ্বিনের দিন যেন আকার ধারণ করিল।’’


এরকম বলার যৌক্তিকতা স্পষ্টতর হয় পরবর্তী বাক্যে, ‘‘কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে, তেমনি এই মেয়েটি আকাশকে, বাতাসকে, আলোককে আপনার চারিদিকে যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিল।’’
‘গল্পগুচ্ছ’-তে ‘রাসমণির ছেলে’ গল্পে দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গে এসেছে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে। পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নতুন পোশাকের আয়োজন আর সেই সূ্ত্রে রাসমণি ও তার গর্ভজাত সন্তান কালীপদর বিচিত্র সম্পর্ক রসায়ন উদ্ভাসিত হয়। যুগপৎ স্বামী ভবানীচরণের সঙ্গে রাসমণির সম্পর্ক বিন্যাসও।

‘‘পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সস্তা কাপড়জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত।’’

এই একটি বাক্যে পরিস্ফুট হয় এক নির্মম সত্য। ভবানীচরণদের আর্থিক দুরবস্থার ইঙ্গিত, তাঁদের অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ইশারা এই বাক্যে পরিষ্কার হয়ে যায়।
আবার দুর্গাপজো উপলক্ষে যে সবাইকার বিকিকিনি, পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অর্থনীতির চালচিত্র এবং সেই চালচিত্রের পেছনে থাকা সাধারণ মানুষের আবেগ ও মনস্তত্ত্ব যে রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না, সেটাও বোঝা যায় এই গল্পের সুতো ধরেই।

‘‘ভবানীচরণের… গুরুপুত্রটি (বগলাচরণ) প্রতিবৎসর পুজোর পূর্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যবসা চালাইয়া থাকেন।”
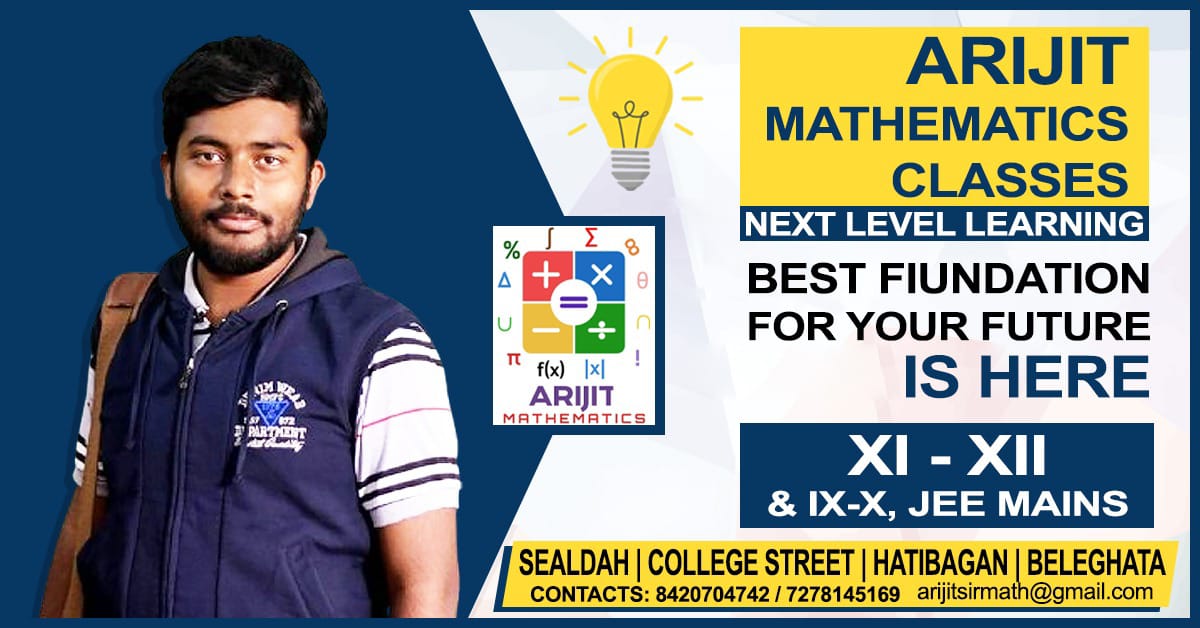
এই ‘সস্তা শৌখিন জিনিসে’র তালিকাটি ভারি বৈচিত্রময়। তাতে আছে অদৃশ্য কালি থেকে শুরু করে কবিতা লেখা পাড়ওয়ালা শাড়ি, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান থেকে শুরু করে ছিপ-ছড়ি-ছাতার একত্র সমবায় ইত্যাদি হরেকরকম জিনিসপত্র। সেসব অদরকারি সস্তার জিনিস ‘গ্রামের নরনারীর মন’ কেন ‘উতলা’ করে দেয়, সেকথা জানাতেও ভােলেন না বাংলা ছোট-গল্পের রূপদক্ষ শিল্পী। ‘‘কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।”

এক কথায়, দুর্গাপুজোর আবহাওয়ায় একটা প্রতিযোগিতার ধারা অন্তঃসলিলা থাকে, ‘Show off’ বা দেখনপনার মাধ্যমে দাম্ভিকতার চোরাস্রোত থাকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের চোখে অগোপন থাকেনি। সেজন্যই তিনি অনায়াসে বুঝে ফেলেন ও বুঝিয়ে দেন, কেন লোকে ক্ষমতার বাইরে গিয়েও পুজোর সময় নানা অপ্রয়োজনীয় সস্তার সামগ্রী বেশি দামে কেনে। নিজেকে জাহির করার এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে চায় না বলেই এমন আচরণ করে। উল্লিখিত বাক্যটি লিখে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন দুর্গাপুজোর সময় সাধারণ মানুষ যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খরচের উৎসবে মেতে ওঠে তার কারণ তাঁদের অজ্ঞানতা নয়, এই আচরণ আদতে তাদের অবধারণগত অসঙ্গতি বা Cognitive dissonance.’। জেনে বুঝেই তারা এমনটা করে থাকে। দুর্গাপুজোর সঙ্গে অন্বিত আর্থ-সামাজিক দিকটাও এভাবে রবীন্দ্র রচনায় নিজস্ব জায়গা খুঁজে নিয়েছে মনস্তত্ত্বের বিন্যাসে।

আবার ‘রবিবার’ গল্পে দুর্গাপুজো রাজনৈতিক বার্তা প্রদানের আশ্রয় হয়ে ওঠে। সেখানে নাস্তিক অভীক যখন ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপুজো করতে উদ্যোগী হয় তখন বিভা তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলে সে নিঃসংশয় চিত্তে বলে ওঠে, ‘‘দেখো বী, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশনালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখো কিন্তু যে দেশে দিবারাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত নাস্তিকেরই। আমি ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।’’ রবীন্দ্রনাথ বিভার মনোবার্তা তুলে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, নাস্তিক অভীক এসব কথা বলে বিভার ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করছে। কিন্তু আমরা টের পাই, এই কথাগুলো অভীকের মুখ দিয়ে বলিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসলে দুর্গাপুজোর মধ্যে নিহিত মিলনের সুরটাকে বাণীবদ্ধ করেছেন। দুর্গাপুজোতে যে তাবৎ সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদ ঘোচানোর ডাক থাকে, সেকথাটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।
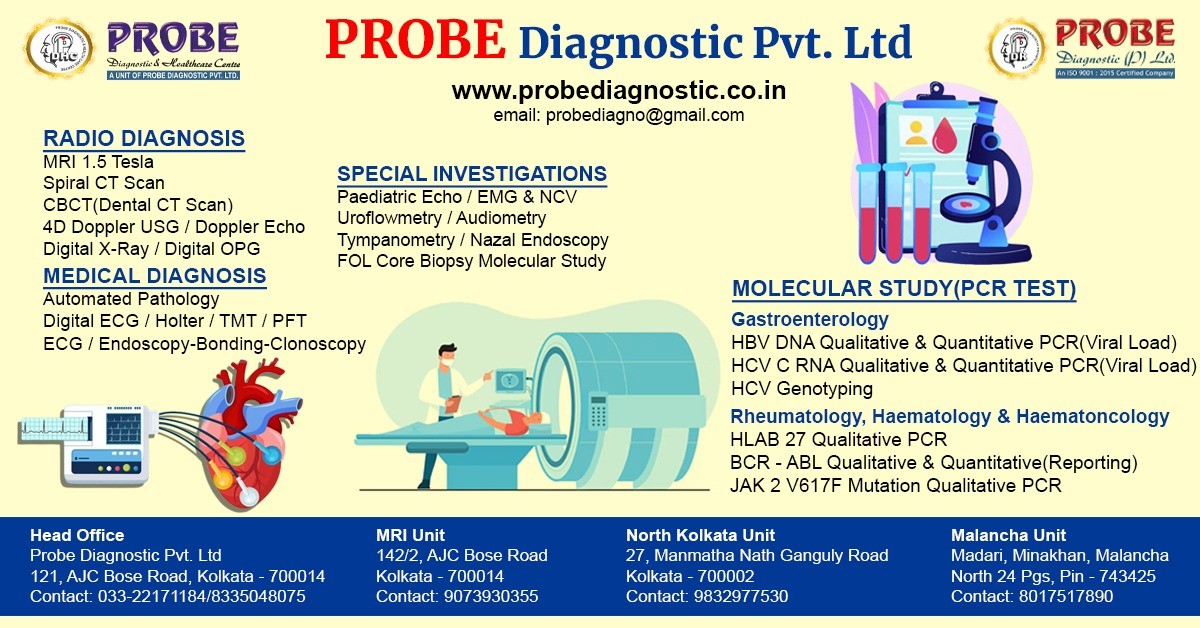
এই গল্পের শেষে দেখতে পাই, অভীকের আর দুর্গাপুজো করা হয়ে ওঠে না। দুর্গাপুজাের চাঁদা আদায়ে ব্রিটিশ ভারতে জুলুম না থাকলেও মিথ্যাচার ছিল যথেষ্ট। সে বিবরণ দিয়ে অভীক বলে, ‘‘তার অজান্তে তারই ক’জন চেলা এক ধনী বিধবা বুড়ির থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করেছে। তাঁকে বুঝিয়েছে, তাঁর রেঙ্গুনবাসী ছেলের প্রাণসংশয় হবে, ‘মা তাকে আস্ত খাবেন’, যদি না বুড়ি দুর্গাপুজোয় যথেষ্ট চাঁদা দিয়ে পাঁঠাবলি ও অন্যান্য উপচারের ক্ষেত্রে আড়ম্বরের ব্যবস্থা করে। এভাবে টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত নাস্তিক অভীকের ভাল লাগেনি। তাই পুজোর জন্য আদায় করা চাঁদা সে উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণার জন্য অমরবাবু যাতে বিলাতে যেতে পারেন, সেজন্য তাঁকে দিয়ে দেয়। তাঁর ভাষায় এ-হল ‘ক্রিমিনাল পুণ্যকর্ম’। পুজো আয়োজনের অর্থ লোকহিতে ব্যয়ের ব্যবস্থা।

‘দেনা পাওনা’ গল্পে আবার দুর্গাপুজো ভিন্ন তাৎপর্যে উল্লিখিত।
পণপ্রথার নিষ্ঠুরতা ফুটিয়ে তোলার কাজে এই গল্পটিতে দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রামসুন্দর তার মেয়ে নিরুপমাকে বিয়ের সময় যথেষ্ট পরিমাণ যৌতুক দিতে পারেনি। সেজন্য তাকে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে নানা অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে। আর মেয়েকেও শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিত হতে হয়েছে। এরকম একটা অস্বস্তিকর প্রেক্ষিতে রামসুন্দর ‘মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেয়াইবাড়ি যাইবেন না।’ কিন্তু দুর্গাপুজোর আগমনি সব হিসাবনিকাশ উল্টে দেয়। ‘‘আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, এবার পুজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে ‘আমি’ খুব একটা শক্তরকম শপথ করিলেন।’’ বাড়িঘর বন্ধক দিয়ে, নাতি নাতনি বৌমাদের যাবতীয় দাবিদাওয়া, পুজোর সময় প্রাপ্তির প্রত্যাশাকে অবহেলা করে রামসুন্দর নিরুপমার পণের টাকা মেটানোর ব্যবস্থা করে ফেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে টাকা আর নিরুপমার শ্বশুরবাড়িতে দেওয়া হয় না। নিরুপমা তাঁকে জানিয়ে দেন নিজের অবস্থান। ‘বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম … তোমার মেয়ের কি কোনও মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এটাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।’ রামসুন্দর বাধ্য হয়ে ফিরে যান। সেদিনটা ছিল দুর্গাপুজোর পঞ্চমী কিংবা ষষ্ঠী। এরপর মাস খানেকের মধ্যে নিরুপমাকে মরতে হয়। আর ‘রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।’
এইভাবে উমার মর্ত্যে আসার প্রহরে বাঙালি পরিবারের, ঘরের উমাদের চিরবিদায়ের লগ্ন সূচিত করে রবীন্দ্রনাথ পণপ্রথার নিষ্ঠুরতাকে বলিষ্ঠতর তাৎপর্যে ফুটিয়ে তোলেন। কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ দেবীপূজার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশিত হওয়ায় পুরো বিষয়টা একটা আলাদা মাত্রা পায়। নারীশক্তির পূজনের লগ্নে নারী নির্যাতনের আলেখ্য মানবমননের বিপ্রতীপ চলনের আবহে তীব্রতর ভঙ্গিমায় উন্মাচিত হয়।
‘স্বর্ণমৃগ’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন পুজো প্রসঙ্গ আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোয়। সেই গল্পে ‘আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী’ হয়। চতুর্থীর দিন থেকে ঘাটে নৌকা লাগে। প্রবাসীদের প্রত্যাবর্তনের সময় সূচিত হয়। দু’হাত ভরে পুজো উপহার নিয়ে তারা ফেরে দলে দলে, কর্মস্থল থেকে বাসস্থলে। তাদের সেই উপহার সামগ্রী সাধারণ হয়েও বিশিষ্ট। তাতে আছে ঝুড়িতে মানকচু, কুমড়া, শুষ্ক নারিকেল, টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতো ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য সুগন্ধী সাবান, নূতন গল্পের বই এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।’

এরই মধ্যে বৈদ্যনাথ ‘নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাংলা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন।’
‘অপদার্থ’ বৈদ্যনাথ তাঁর দুই ছেলের জন্য পুজোয় উপহার নিজে হাতে তৈরি করেন। কাঠ দিয়ে বানানো দুখানা নৌকা। ‘ছেলেদের আনন্দ কলরবে আকৃষ্ট হয়ে (বৈদ্যনাথ জায়া) মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার’ দেখেন। তারপর ‘রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলনা দুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।’

চিরায়ত দরিদ্র বাংলার বাবার পুজো উপহার এভাবেই আর্থ-সামাজিক তাড়নায় বৈভবের বিপরীতে প্রত্যাখ্যাত ও উপেক্ষিত হওয়ার জায়গা খুঁজে নেয়। দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে সমাজ বিশ্লেষকের ভূমিকায় অনন্য হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা ‘বুর্জোয়া অলিয়েনেশন’-এর অভিযোগ অভিঘাত থেকে সরে আসার প্রত্যয় অর্জন করে নেয়।
শুধু গদ্যভাষার আঙ্গিকে নয়, ছড়ায় কবিতায় গানে, ছন্দোবদ্ধ ভাষার বিভঙ্গেও রবীন্দ্র সাহিত্য দুর্গাপুজােকে বিশিষ্ট পরিসর ছেড়ে দিয়েছে। বৈচিত্র্যময়তা সেই পরিসরেও অনবদ্য বিশিষ্টতা।
রবিকবি যখন লেখেন, ‘‘আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি/ পূজার সময় এল কাছে। / মধু বিধু দুইভাই ছুটাছুটি করে তাই আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে।’’ তখন পুজোর সাজের আনন্দ-বেদনা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে।
আবার যখন তিনিই লেখেন, ‘‘আনন্দময়ীর আগমনে, / আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে। / হেরো ওই ধনীর দুয়ারে। দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।’’ তখন টের পাওয়া যায় রবিকবি আসলে ছন্দোবদ্ধ মাধুরী ঢেলে একটা গল্প লিখতে চাইছেন। সেটা সুখ-দুঃখের গল্প, আনন্দ-বেদনার গল্প, হাসি-কান্নার হিরে পান্না দিয়ে সাজানো এক শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ের গল্প।
‘যেতে নাহি দিব’ কবিতায় পূজাবসানে কর্মব্যস্ত জীবনে পুনঃপ্রবেশের ইশারায় সাড়া দেওয়ার তাগিদ কিংবা বাধ্যবাধকতা সুস্পষ্ট। ‘‘গিয়েছে আশ্বিন পূজা ছুটির শেষে / ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূরদেশে/ সেই কর্মস্থানে।’’
আবার ‘ছুটির আয়োজন’ ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারেও এই কবির অনায়াস দক্ষতা। তিনি লেখেন, ‘‘কাছে এল পুজোর ছুটি। / রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ। / … আকাশের কোণে কোণে সাদামেঘের আলস্য, / দেখে মন লাগে না কাজে।’’

‘আগমনী’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙালির ঘরের মেয়ে উমার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ। ‘‘আজ মেনকার আদরিণী উমা/ আসিবে বরষ-পরে। / তাইতে আজিকে হরষের ধ্বনি/ উঠিয়াছে ঘরে-ঘরে।’’
ভারতমাতাকে মা দুর্গার সঙ্গে এক করে দেখার ব্যাপারে আপত্তি ছিল তাঁর নিখিলেশের। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে তাই নিখিলেশ দুর্গামূর্তিতে অন্য ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিল, সে বলেছিল, দুর্গা ‘পলিটিক্যাল দেবী’। বিধর্মীদের শাসনকালে বাঙালি দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর প্রার্থনা করেছিল। এই দেবী সেই কামনার বাহ্যরূপ।
এর বিপ্রতীপ অবস্থানে অধিষ্ঠান সন্দীপের। সে ভাবে ও বলে, ‘‘কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে (এসব কথা) বলতে পারলে। … (নিখিল বলে) দেশ দেবী নয়, তাই (দেবীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে স্রেফ মন্ত্র পড়ে কাঙ্ক্ষিত ফল কামনায়) ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেই দিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।’’
এই প্রেক্ষিতে সন্দীপের স্থির অনুভব, ‘‘কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনায় ভাল।’’ কিন্তু সন্দীপের নিজের কথা তো আর স্রেফ কাগজে লেখিবার নয়। সেকথা পণ্ডিত যেরকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে, সেরকম বিষয় নয়। ‘লাঙলের ফলা দিয়ে চাষি যেরকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে’ সেভাবেই সন্দীপ দেশমাতৃকার আরাধনা ও বন্দনা করতে চায়।
নিখিলের ভাবনায় রাবীন্দ্রিক অনুভব। সন্দীপের কামনায় দেশভক্তির স্থূল প্রকাশে তিনি অনুপস্থিত।
তাই ভারতমাতা দুর্গামাতা তাঁর দৃষ্টিতে অভিন্নরূপা নন। দেবী দুর্গাকে দেশমাতৃকা হিসেবে বন্দনা করতে তাঁর মন সায় দেয়নি।
তা বলে সমাজমনস্ক সৃজনকার হিসেবে তিনি বাঙালির প্রাণের দেবীকে তাঁর রচনার বৃত্ত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেও পারেননি।
দুর্গাপুজো তাই বিশিষ্ট প্রাসঙ্গিকতায় রবীন্দ্র রচনাসম্ভারে আপন আসন খুঁজে নিয়েছে।
সার্বজনীনতা ও প্রাতিস্বিকতার অনবদ্য মেলবন্ধনে দুর্গাপূজোর উপস্থাপনা রবীন্দ্র রচনাবলয়ে তাই অনন্যভাবে প্রতত।
আরও পড়ুন- আমার বলার কিছু আছে
















